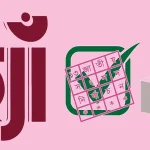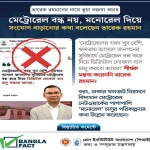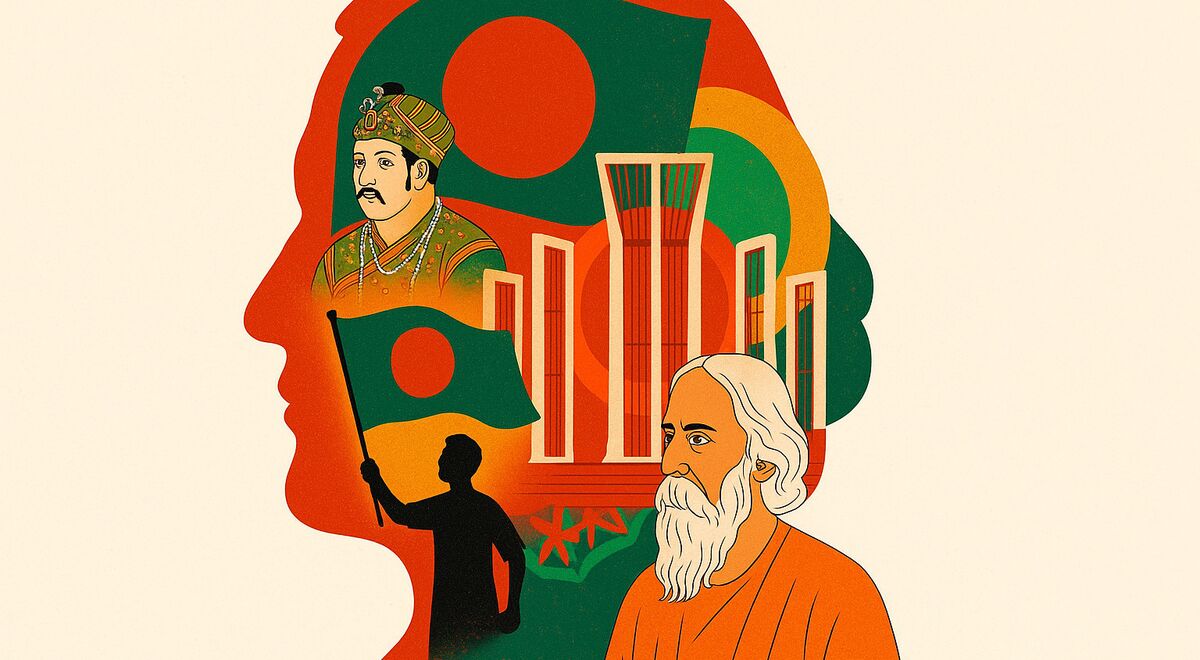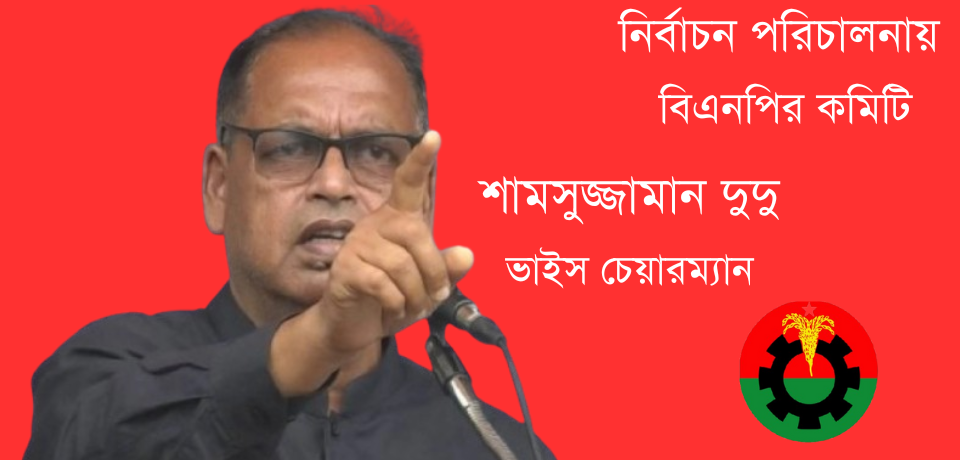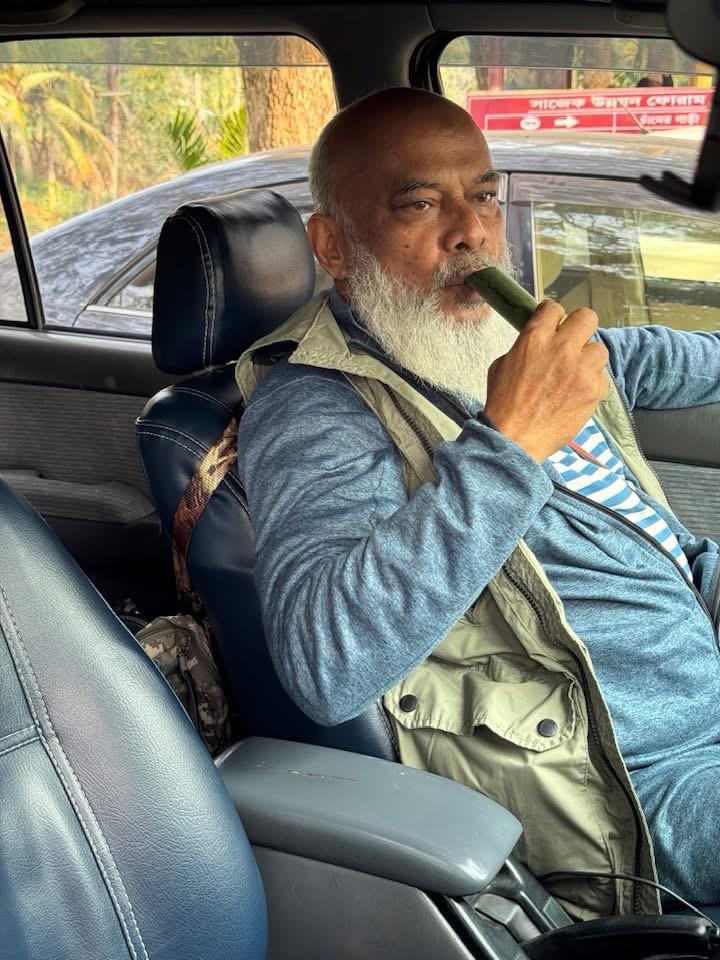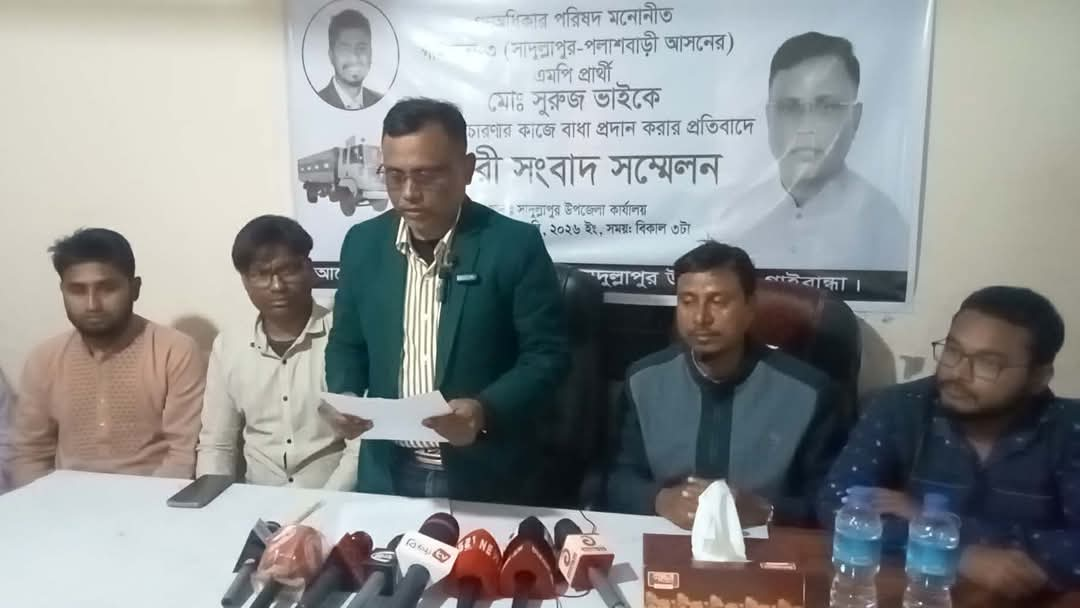||এমএম আকাশ ||
দেশ নির্বাচনের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে অনুষ্ঠিত হবে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক দল ও সংশ্লিষ্ট মহলে ব্যাপক আলোচনা চলছে। আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে আগ্রহ আছে। মানুষ চায় ঠিকমতো ভোট দিয়ে একটি নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় আসুক। ৯ অক্টোবর বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) সভায় পরিকল্পনা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেছেন, এ মুহূর্তে সবকিছুর ঊর্ধ্বে দরকার একটি সুষ্ঠু নির্বাচন। কিন্তু সুষ্ঠু নির্বাচনের কয়েকটি শর্ত আছে। অন্যতম একটি শর্ত হচ্ছে প্রার্থীদের মধ্যে যাতে বিশেষ দলের বিশেষ প্রার্থীদের অর্থশক্তি বা পেশিশক্তি অত্যধিক না হয়। এক প্রার্থী জামানতের টাকা বা মনোনয়ন ফিই জোগাড় করতে পারলেন না, অন্যদিকে আরেক প্রার্থী কোটি টাকা পকেটে নিয়ে মাঠে নামলে নির্বাচনের ফলাফল ভালো হবে না। কালো টাকার মালিকরা কালো টাকা বিনিয়োগ করে সংসদকে আবারো ধনী ও অসৎ ব্যবসায়ী-আমলা-রাজনীতিবিদদের ক্লাবে পরিণত করবে। অবশ্য ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ জানেন, আমরাও জানি ক্রোনি ক্যাপিটালিজমের অধীনে দরিদ্র অর্ধভুক্ত, অশিক্ষিত, অসচেতন ভোটারদের পক্ষে ভয়-ভীতি-লোভের ঊর্ধ্বে উঠে ভোট দেয়া প্রায় অসম্ভব।
তার পরও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনকে এমন কিছু ন্যূনতম সংস্কার কার্যকর করতে হবে যাতে অর্থের খেলা যথাসম্ভব কমানো যায়। নির্বাচন নিয়ে নানামুখী আলোচনা হলেও নির্বাচন কীভাবে অবৈধ অর্থের প্রভাবমুক্ত করা যাবে তা নিয়ে কারো মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। অথচ নির্বাচন যদি অর্থের প্রভাবমুক্ত করা না যায় তাহলে সেই নির্বাচন কখনই জনপ্রত্যাশা পূরণ করবে না।
সাংবিধানিক দিক থেকে বাংলাদেশ গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। অর্থাৎ রাষ্ট্রের মালিক সাধারণ জনগণ। সরকার হচ্ছে জনগণের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত। দেশের অধিকাংশ মানুষ হচ্ছে শ্রমিক, কৃষক, দিনমজুর তথা নিম্নবিত্ত। আর্থিকভাবে তারা দুর্বল। সাধারণ মানুষ অর্থাৎ যারা রাষ্ট্রের মালিক তাদেরই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণের কথা। কিন্তু দেশের প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিত্তহীনদের পক্ষে নেতা হওয়া বা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করা কঠিন। দেশের নির্বাচন প্রক্রিয়াই এমন যে সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গেলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। সাধারণ দরিদ্র মানুষের পক্ষে এ বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা কঠিন। ফলে যোগ্য ও জনপ্রিয় অনেক ব্যক্তির পক্ষে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয় না। ফলে সাধারণ মানুষ বাধ্য হয়ে কোনো বিত্তবান ব্যক্তিকে ভোট দিয়ে নির্বাচনে জয়ী করে ও তাকে নেতা মেনে নেয়। রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই অথচ বিত্তবান এমন ব্যক্তি নেতা হলে অর্থনীতিশাস্ত্রের ভাষায় প্রিন্সিপাল-এজেন্ট সমস্যা দেখা দেয়। অর্থাৎ মালিক-প্রতিনিধির মধ্যে সম্পর্কের সমস্যা দেখা দেয়। দেশের মালিক জনগণ কিন্তু দেশ চালায় মালিকের প্রতিনিধিরা, যাদের আবার নিজস্ব সংকীর্ণ স্বার্থের প্রতিই মনোযোগ বেশি। যেমন গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জমির মালিক জমি চাষ করেন না। জমি চাষ করেন বর্গাচাষীরা। মালিক জমি চাষ করলে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতি যতটা আন্তরিকতা থাকে বর্গাচাষীর মাধ্যমে জমি চাষ করা হলে সে আন্তরিকতা থাকে না। তবে বর্গাচাষী নিজেরাও গরিব বলে নিজেদের খোরাকির জন্য বাধ্য হয়ে মালিকের জমি সর্বোচ্চ পরিশ্রম করে চাষ করেন। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে যেহেতু রাষ্ট্রের প্রকৃত মালিক দূরে দুর্বল অবস্থানে থাকেন এবং তাদের প্রতিনিধি হিসেবে বিত্তবান শ্রেণীর মানুষরাই জবাবদিহিবিহীনভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করে থাকেন, তাই সে অবস্থায় জনকল্যাণের বিষয়টি উপেক্ষিত হয়। বিত্তবান শাসকশ্রেণী সাধারণ মানুষের কল্যাণের পরিবর্তে গোষ্ঠী স্বার্থ উদ্ধারে বেশি তৎপর থাকেন। জনগণ বা আপামর ভোটার যারা দেশের মালিক তাদের স্বার্থ এক রকম আর যারা নিজেরাই ধনী ব্যবসায়ী বা তাদের থেকে টাকা নিয়ে নির্বাচনী বৈতরণি পারি দিয়েছেন তাদের স্বার্থ কখনই এক রকম হতে পারে না। এখানে স্বার্থের সংঘাত দেখা দেয়। বিশেষ করে অসৎ রাজনৈতিক নেতারা যখন অসৎ লোকের কাছ থেকে কালো টাকা নিয়ে বিনিয়োগ করে নির্বাচনে জয়লাভ করেন তখন তাদের প্রাথমিক ও মূল উদ্দেশ্য থাকে নির্বাচনে ব্যয়িত অর্থ সুদে-আসলে তুলে নেয়া। কিছু মানুষের কাছে নির্বাচন এখন সবচেয়ে লাভজনক বিনিয়োগ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারলে ক্ষমতার পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জনের সুযোগ থাকে। কেউ যদি ১০ কোটি টাকা ব্যয় করে নির্বাচনে জয়লাভ করে তাহলে তার প্রচেষ্টা থাকবে কীভাবে মেয়াদকালে অন্তত ১০০ কোটি টাকা আয় করা যায়। এটা একটি নিষ্ঠুর চক্র।
নির্বাচনে টাকার খেলা বন্ধ করা খুবই কঠিন। কারণ এটা আমাদের মতো পুঁজিবাদী দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থায় একটি প্রচলিত ধারায় পরিণত হয়েছে। আমরা যদি নির্বাচন ব্যবস্থাকে বৃহৎ ধনিক গোষ্ঠীর বৈধ-অবৈধ অর্থের প্রভাবমুক্ত করতে চাই, তাহলে রাষ্ট্রের যারা মালিক তারা যাতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেন, প্রতিযোগিতায় তাদের জন্যও যাতে উন্মুক্ত জায়গা থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু শ্রেণীবিভক্ত সমাজে রাষ্ট্রের যারা মালিক তাদের হাতে নির্বাচনে কারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন সে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নেই। এটা নির্ধারণ করেন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতারা। রাজনৈতিক দলের নেতারা এমন ব্যক্তিকেই নির্বাচনে মনোনয়ন দান করেন যারা প্রচুর পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে পারবেন। দেখা যায় যারা এক সময় অন্য পেশায় ছিলেন, যেমন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা, সরকারি চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী—তারা নির্বাচনের আগে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে থাকেন। প্রশ্ন হলো তারা তাদের এত দিনের অভিজ্ঞতা, পেশাগত দক্ষতা পরিত্যাগ করে রাজনীতিতে কেন আসেন? মূলত তারা দুটি কারণে রাজনীতিতে আসতে চান। প্রথমত, রাজনীতিতে যুক্ত হলে রাজনৈতিক পলিসিকে তারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। রাজনৈতিক পলিসিকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সমাজ বিপন্ন করার কোনো ইচ্ছা তাদের থাকে না, তারা তাদের নিজেদের ও বন্ধুদের ব্যবসায়িক এবং অন্যান্য স্বার্থ উদ্ধার করতে সচেষ্ট হন। এছাড়া রয়েছে ক্ষমতার মোহ। তারা মনে করেন, তারা যদি মন্ত্রী হতে পারেন বা একজন এমপি হতে পারেন তাহলেও বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হতে পারবেন। ক্ষমতা ও অর্থের মোহ কাটানো খুবই কঠিন। যারা বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে নির্বাচনে জয়লাভ করেন জনগণের সেবা করার মতো উদ্দেশ্য বা মনোভাব তাদের থাকে না বললেই চলে। তবে ব্যতিক্রম নেই, সেটি আমি বলব না। সে রকম সামাজিক ধনী উদ্যোক্তারা সংসদ সদস্য হওয়ার জন্য উদগ্র হন না।
নির্বাচনে টাকার খেলা থেকে মুক্তি পাওয়া বেশ কঠিন হলেও একেবারে অসম্ভব নয়। আমাদের এমন কিছু ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে অবসরপ্রাপ্ত আমলা, অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা ও ধনী ব্যবসায়ীরা নির্বাচনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে নিরুৎসাহিত হন। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলো শীর্ষ নেতৃত্বকে সঠিক পদ্ধতিতে প্রার্থী মনোনয়নের দায়িত্ব নিতে হবে। নির্বাচনে মনোনয়ন দানকালে বিত্তবানদের পরিবর্তে দলের একনিষ্ঠ কর্মী, যারা দীর্ঘদিন ধরে দলের কর্মকাণ্ডে যুক্ত রয়েছেন, যারা এলাকার ভূমিপুত্র ও যাদের বিরুদ্ধে নৈতিক স্খলনের কোনো অভিযোগ নেই তাদের মনোনয়ন দিতে হবে, যদিও তারা বিত্তবান নন। অর্থাৎ যারা তৃণমূল পর্যায় থেকে উঠে এসেছেন তাদেরই নির্বাচনে মনোনয়ন দিতে হবে। বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক দলগুলোর এক শ্রেণীর নেতার বিরুদ্ধে মনোনয়ন বাণিজ্য করার অভিযোগ শোনা যায়। এটা বন্ধ করতে হবে। বিগত সময়ে কবি নির্মলেন্দু গুণ যখন আওয়ামী লীগের নির্বাচনী বোর্ডে সাংসদ পদে মনোনয়নের জন্য সাক্ষাৎকার দিতে গিয়েছিলেন তখন তার সামান্য ব্যাংক ব্যালান্সের কথা শোনার পর তাকে সেদিন আর মনোনয়ন দেয়া হয়নি!
রাজনৈতিক দলের যেসব নেতা ইউনিয়ন কাউন্সিল অথবা অন্য কোনো স্থানীয় পরিষদ নির্বাচনে জয়লাভ করে জনসেবা করেছেন তাদের সংসদ সদস্য নির্বাচনে মনোনয়নদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে। যদি তৃণমূল পর্যায়ের রাজনৈতিক কর্মী বা নেতাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হয় তাহলে নির্বাচনী ব্যয় কমাতে হবে। মনোনয়ন ফি ৫ হাজার টাকা করা যেতে পারে। মনোনয়ন ফি যদি ৫০ হাজার টাকা বা তারও বেশি হয় তাহলে অনেকের পক্ষেই মনোনয়নপত্র ক্রয় করা সম্ভব হয় না। ১৯৭২ সালের আরপিও (রিপ্রেজেনটেশন অব দ্য পিপলস অর্ডার বা জনপ্রতিনিধিত্ব আদেশ) অনুযায়ী কোনো দলের ২০০ প্রার্থীর অধিক প্রার্থী থাকলে তাদের জন্য সর্বোচ্চ অনুমোদিত দলীয় মোট নির্বাচনী খরচের সীমারেখা নির্ধারণ হয়েছিল ৪ দশমিক ৫ কোটি টাকা। তাতে দেখা যায় ৩০০ প্রার্থীর জন্য ৪ দশমিক ৫ কোটি টাকা ব্যয় ধরলে গড়ে একজন প্রার্থীর অনুমোদিত সর্বোচ্চ ব্যয়সীমা তখন ছিল মাত্র ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা।
কিন্তু বর্তমানে নিয়মানুযায়ী প্রার্থী একাই ব্যক্তিগতভাবে ২৫ লাখ টাকা খরচ করতে পারবেন! এছাড়া যেসব দল ১০০-২০০ প্রার্থী মনোনয়ন দেবেন তারা দলীয়ভাবে আরো ৩ কোটি টাকা খরচ করতে পারবেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এ দরিদ্রবহুল দেশে (বর্তমানে প্রায় ২৭ শতাংশ মানুষ দরিদ্র—পিপিআরসির হিসাব অনুসারে) সর্বোচ্চ নির্বাচনী খরচ দাঁড়াবে প্রায় ২৫ লাখ (ব্যক্তিগত) ও ৩ লাখ (দলীয়)—মোট ২৮ লাখ টাকা! ডেইলি স্টারের ৮ অক্টোবরের রিপোর্ট থেকে আরো জানা যায় ২০১৮ সালে যে নির্বাচন হয়েছিল সেখানে আওয়ামী লীগ দলগতভাবে খরচ করেছিল ২৬১ প্রার্থীর জন্য মোট ১ কোটি ৫ লাখ টাকা। বিএনপি ২৬১ প্রার্থীর জন্য খরচ করেছিল ১ কোটি ১১ লাখ টাকা আর ইসলামী আন্দোলন করেছিল ২৯৮ প্রার্থীর জন্য ২ কোটি ১৪ লাখ টাকা।
নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য প্রচার-প্রচারণা চালাতে হয়। এ খাতে বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হয়। যারা বিত্তবান তারা প্রচারকার্যে বিপুল অর্থ ব্যয় করেন। কিন্তু যারা দরিদ্র পরিবার থেকে আগত তারা নির্বাচনী প্রচারকাজে তেমন একটা অর্থ ব্যয় করতে পারেন না। ফলে তারা প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে জনগণের নিকটবর্তী হতে পারেন না। গণমাধ্যমের কভারেজ কম পান। দরিদ্র-ধনী নির্বিশেষে প্রচারণার জন্য পোস্টার-ব্যানার সরকারি খরচে মুদ্রণ করে দেয়া যেতে পারে। আর প্রার্থীদের জন্য সরকারি খরচে একক মঞ্চ তৈরি করে সেখানে সব প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে স্ব-স্ব বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ করে দেয়া যেতে পারে। তাতে অর্থব্যয়ের অশ্লীল প্রতিযোগিতা কিছু কমতে পারে।
১৯৯১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে উপদেষ্টা রেহমান সোবহানের তত্ত্বাবধানে নাজমা চৌধুরীর নেতৃত্বে ‘রাজনৈতিক দলের’ ওপর যে টাস্কফোর্স গঠিত হয় সেখানে আমি, আনু মুহাম্মদ, আহমেদ কামাল ও মুশতাক খান (সোয়াস-ইংল্যান্ড) সম্মিলিতভাবে সুপারিশ করেছিলাম যে মূল সংসদীয় নির্বাচনী প্রচারণা সভাটি এলাকায় নিজ খরচে রাষ্ট্র আয়োজন করবে। যারা নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করবে তারা সেই মঞ্চে গিয়ে বিতর্ক করবে। রেডিও-টেলিভিশনে প্রার্থীদের বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ করে দেয়া হবে। এটা করা হলে নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে যে বৈষম্য সৃষ্টি হয় তা দূর হতে পারে। ভোটারদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য প্রচারণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু প্রচলিত নির্বাচনী ব্যবস্থায় যারা দরিদ্র প্রার্থী তারা প্রচারণার ক্ষেত্রে সব সময়ই পিছিয়ে থাকেন। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে প্রার্থীদের প্রচার-প্রচারণার সুষম ব্যবস্থা করে দেয়া গেলে প্রচারণার ক্ষেত্রে যে বৈষম্য সৃষ্টি হয় তা দূর হবে। গণতান্ত্রিক সহনশীলতা ও যুক্তি চর্চা বাড়বে—নির্বাচনী খরচও কমে যাবে। কিন্তু আমাদের সেই পরামর্শ বা সংস্কার প্রস্তাব কোনো রাজনৈতিক দলই পরবর্তী সময়ে গ্রহণ করেনি। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়ে সংস্কার বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক হলেও নির্বাচনী সংস্কারের এ অর্থনৈতিক দিকটি নিয়ে কোনো কথাবার্তা হচ্ছে না। নতুন নতুন রাজনৈতিক দল নির্বাচন নিয়ে নানা ধরনের কথা বলছে। কিন্তু কায়েমি শ্রেণী স্বার্থগুলোকে কীভাবে একটু দুর্বল করা যায় তা নিয়ে কেউ ভাবছে না। অথচ এখানে অগ্রগতিটাই ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।
এখনো আরপিও বিধান করা যেতে পারে যাতে রাজনৈতিক দলগুলো অর্থের বিনিময়ে যে কাউকে মনোনয়ন দিতে না পারে। কেউ নির্বাচনের এক বছর বা দুই বছর আগে ব্যবসা, সরকারি উচ্চ পেশা ইত্যাদি ত্যাগ করে মওকা আদায়ের জন্য নব্য রাজনীতিতে যোগদান করলে অথবা কারো বিরুদ্ধে যদি অতীতে ‘মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ’ থাকে সে এসে নির্বাচনে দাঁড়ালে বা যিনি সদ্য অতীতে ‘ঋণখেলাপি’ তিনি টাকা আংশিক শোধ করার পর মনোনয়ন দিলে তারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। একজন প্রার্থীকে নির্দিষ্ট সময় জনসেবা করে নিজেকে প্রমাণ করার পরই তাকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ দেয়া যেতে পারে। মহান রাজনীতির ব্রত গ্রহণের ক্ষেত্রে আচরণগত বাধ্যবাধকতা/পূর্বশর্ত থাকা উচিত।
যারা বিভিন্ন দায়িত্বে আছেন তাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হলে স্বীয় পদ থেকে পদত্যাগ করতে হবে। যারা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান থেকে অবসর গ্রহণ করে নির্বাচনে অংশ নেন তাদের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়া যেতে পারে। কেউ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চাইলে তাকে অবসর গ্রহণের অন্তত ৫ বছর অপেক্ষা করার বিধান করা যেতে পারে। রাজনীতি হতে হবে জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা ও জনসেবার জন্য। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের চাকরি থেকে অবসর গ্রহণকারী কোনো ব্যক্তি যদি নির্বাচনে অংশ নিতে চান তাহলে তাকে পেনশন সুবিধা সারেন্ডার করতে হবে এমন একটি আইনি বাধ্যবাধকতা আরোপ করা যেতে পারে। রাজনীতি ও নির্বাচন হতে হবে একান্তই জনসেবার জন্য, রাষ্ট্র থেকে সুবিধা আদায়ের জন্য নয়। কারো আর্থিক অথবা প্রশাসনিক ক্ষমতা বৃদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে রাজনীতিকে ব্যবহারের প্রবণতা বন্ধ করতে হবে। রাজনীতি হতে হবে রাজনীতিবিদদের জন্যই। কেউ যাতে বাইরে থেকে এসে হঠাৎ করেই রাজনীতিবিদ বনে যেতে না পারেন তা নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচনে সবার জন্য সমান সুযোগের কথা শুনি। নির্বাচনে অর্থের ব্যবহার বন্ধ করা না গেলে কোনোভাবেই সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব নয় এবং রাজনীতির মর্যাদা পুনরুদ্ধারও সম্ভব নয়।
বর্তমানে একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ তিনটি নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। এটা আইনসম্মত নয়। কারণ একজন প্রার্থীকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হলে তাকে অবশ্যই সেই নির্বাচনী এলাকার ভোটার হতে হয়। একজন ব্যক্তি নিশ্চয়ই তিনটি এলাকা থেকে ভোটার হতে পারেন না। এছাড়া কেউ একজন তিনটি নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বিজয়ী হলেও পরবর্তী সময়ে তাকে দুটি আসন ছেড়ে দিতে হয়। পরবর্তী সময়ে ছেড়ে দেয়া দুটি আসনে উপনির্বাচন আয়োজন করতে হয়। এতে রাষ্ট্রের বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হয়। একজন প্রার্থীকে একটি মাত্র আসন থেকে নির্বাচনে অংশ নিয়ে তার জনপ্রিয়তা যাচাই করতে হবে। কারো ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা কত বিস্তৃত তা প্রমাণের অন্য অনেক উপায় আছে। ব্যক্তিগত অহং মেটানোর জন্য রাষ্ট্রীয় অর্থের অপচয় না হওয়াই উচিত।
এমএম আকাশ: অর্থনীতি ও রাজনীতি বিশ্লেষক
সুত্র ঃ বণিক বার্তা