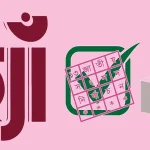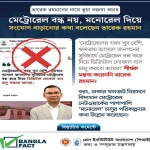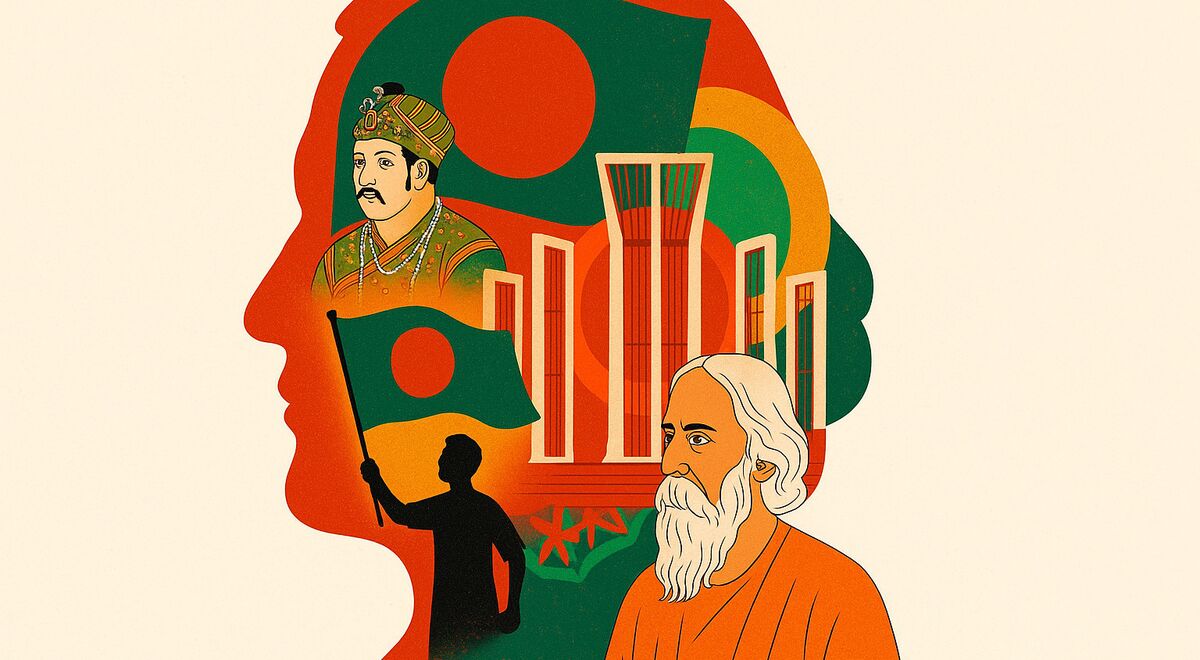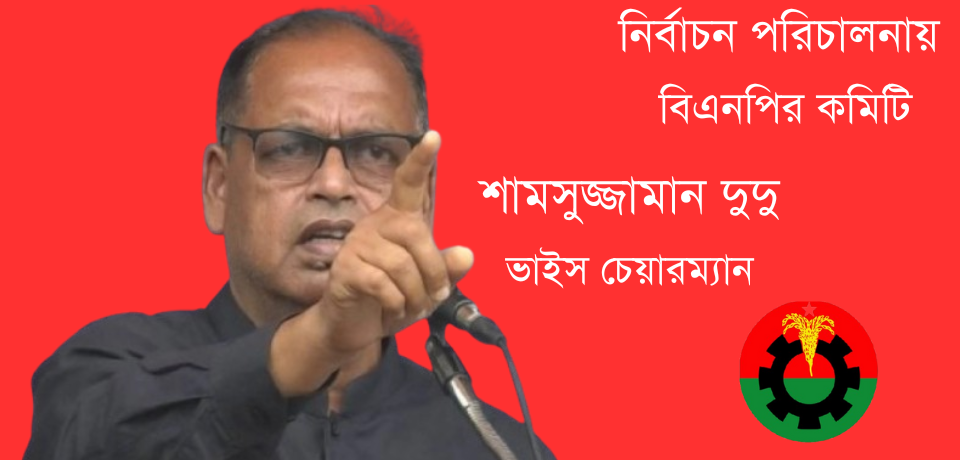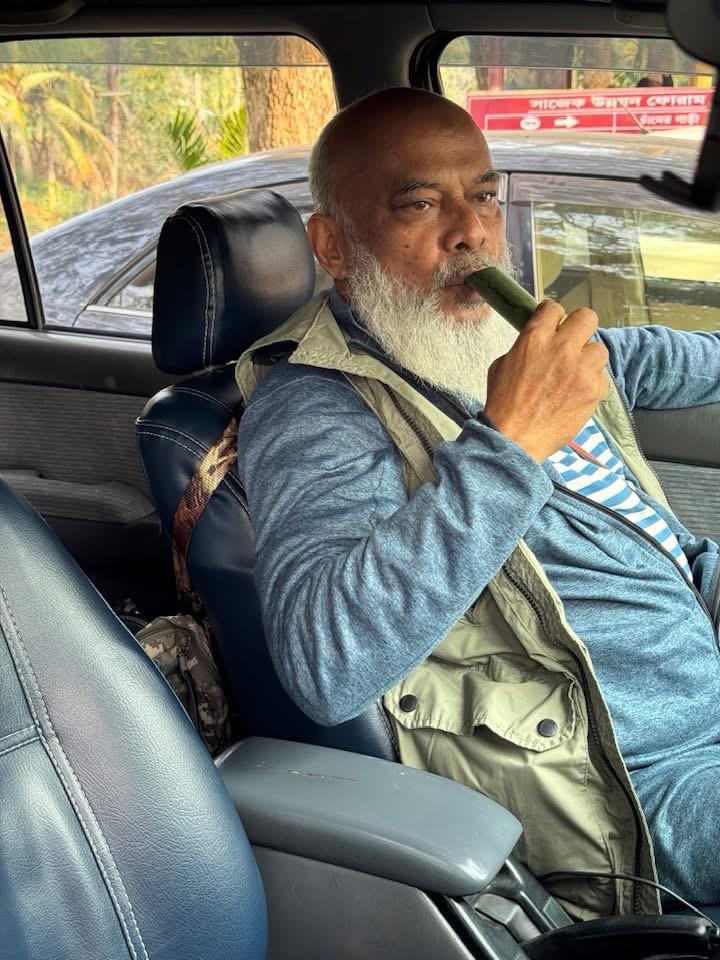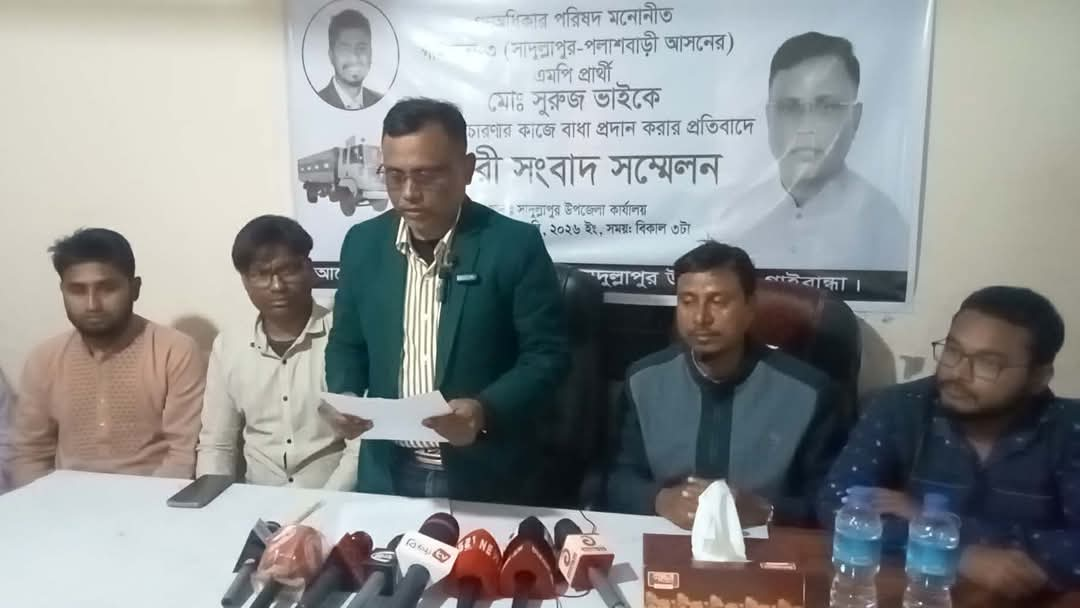||সানাউল্লাহ সাগর||
নির্বাচন ঘিরে এখন যে আলোচনাগুলো চলছে, তার কেন্দ্রবিন্দু হলো নির্বাচনী জোট গঠন। কারণ আগামী জাতীয় নির্বাচন গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ দিক উন্মোচন করবে। একদিকে বিএনপি, অন্যদিকে জামায়াত- এই দুই দলকেন্দ্রিক রাজনীতির বাইরে এখন আবার একাধিক নতুন ও পুরনো শক্তি নিজস্ব অবস্থান পুনর্নির্ধারণের চেষ্টা করছে। নির্বাচনের সময় যত ঘনিয়ে আসছে, ততই জোট গঠনের আলোচনা তীব্র হচ্ছে। পুরনো দল থেকে শুরু করে সদ্য গঠিত রাজনৈতিক দল- সবাই এখন নিজেদের হিস্যা বুঝে নিতে ব্যস্ত। একদিকে ক্ষমতার পালাবদলের প্রত্যাশা, অন্যদিকে রাজনীতিতে টিকে থাকার লড়াই। এই দুই মেরুর টানাপড়েনে এখন রাজনীতির মাঠ উত্তপ্ত।
দীর্ঘ সময় ধরে রাজপথে আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে পতিত হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া বিএনপি এখন নির্বাচনের দ্বারপ্রান্তে এসে জোট রাজনীতি নিয়ে নতুনভাবে ভাবছে। আগের মতো জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে জোটে যাচ্ছে না। বিএনপি একটি বৃহত্তর গণতান্ত্রিক জোট গঠনের পথে এগোচ্ছে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন। এই জোটের উদ্দেশ্য কেবল নির্বাচনে অংশগ্রহণ নয়, বরং একটি বিকল্প রাজনৈতিক মঞ্চ তৈরি করা, যা আগামী নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করতে পারে এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় সফল হতে পারে।
বিএনপির মূল কৌশল হলো দলীয় কাঠামো শক্তিশালী করা এবং আন্দোলনের অংশীদার শক্তিগুলোকে একটি প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসা। সেই পরিপ্রেক্ষিতে তারা গণতন্ত্র মঞ্চ, এনসিপি, এবি পার্টি, গণঅধিকার পরিষদসহ বিভিন্ন দলের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে। নতুন রাজনৈতিক দল এনসিপি বাদে এসব দলের অধিকাংশই বিএনপির সঙ্গে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে ছিল। তবে আনুষ্ঠানিক জোটে ছিল না। ফলে আসন্ন নির্বাচনে একটি নতুন গণতান্ত্রিক ঐক্যফ্রন্ট বা জনজোট গঠনের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে বিএনপির জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো জামায়াতে ইসলামীর ভোটব্যাংক ও সাংগঠনিক প্রভাব থেকে নিজেদের দূরে রেখে বড় পরিসরে ভোট একত্রিত করা। কারণ দীর্ঘ সময় ধরে বিএনপি ও জামায়াত নির্বাচনী মাঠে জোটবদ্ধ ছিল। ফলে বিএনপি হয়তো আনুষ্ঠানিক না হলেও পরোক্ষ সমঝোতার পথে যেতে পারে। যাতে ইসলামি ভোটও তাদের পক্ষে থাকে, কিন্তু আনুষ্ঠানিক জোটের দায় বহন না করতে হয়।
আবার ২০২২ সালে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের মাঠে তৈরি হওয়া গণতন্ত্র মঞ্চের ভূমিকাও ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। নাগরিক ঐক্য, গণসংহতি আন্দোলন, রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন, জেএসডি, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ও ভাসানী জনশক্তি পার্টি- এই ছয় দল মিলে গঠিত গণতন্ত্র মঞ্চ এখন নিজেদের প্রসার ঘটাতে চাইছে। তারা চায় বিএনপি ও জামায়াতের ছায়ার বাইরে থেকে একটি স্বতন্ত্র রাজনীতির বৈধ ও গণতান্ত্রিক বিকল্প হয়ে উঠতে। তাদের নীতি হলো রাষ্ট্র পুনর্গঠন, গণতান্ত্রিক সংস্কার ও নাগরিক স্বাধীনতা। এই জোটে ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের শক্তি এবি পার্টি, গণঅধিকার পরিষদ, এনসিপি ও আপ বাংলাদেশও যুক্ত হতে পারে।
অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বে একটি বৃহত্তর ইসলামি জোট গঠনের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে বলে শোনা যাচ্ছে। এই জোটে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, ইসলামী ঐক্যজোটসহ আরও কিছু আঞ্চলিক ইসলামি দল। তাদের লক্ষ্য হলো ইসলামি ভোটব্যাংককে একত্রিত করে নির্বাচনে একটি দৃশ্যমান শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হওয়া। হাসিনা সরকারের পতনের পর জামায়াত তাদের ভোটার ভিত্তি মাঠপর্যায়ে আগের তুলনায় আরও বিস্তৃত ও জনবান্ধব করে তোলার চেষ্টা করছে। বিশেষ করে গ্রামীণ মধ্যবিত্ত ও ধর্মনিষ্ঠ ভোটারদের মধ্যে তাদের প্রভাব দেখা যাচ্ছে। ফলে এই জোট নির্বাচনের রাজনীতিতে ৫০-৭০ আসনের সমীকরণে প্রভাব ফেলতে পারে। তবে ইসলামি রাজনীতির সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো, তারা এখনও গণতান্ত্রিক রাজনীতির ভাষা খুঁজে পায়নি। রাজনৈতিকভাবে ইসলামকে গণ-আন্দোলনের রূপ দিতে ব্যর্থ হওয়ায় তাদের প্রভাব অনেকাংশে প্রতীকী পর্যায়ে সীমাবদ্ধ। তবুও ইসলামি ভোটব্যাংকের সম্ভাব্য দিকনির্দেশনা আগামী নির্বাচনের ফল নির্ধারণে ভূমিকা রাখবে, এতে সন্দেহ নেই।
বাংলাদেশের বাম রাজনীতি দীর্ঘদিন ধরেই ছিন্নমূল ও বিভক্ত। কিন্তু এবারের নির্বাচনে কিছুটা নতুন সমন্বয়ের চেষ্টা দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) নেতৃত্বে একটি নির্বাচনমুখী জোট গঠনের আলাপ চলছে। সিপিবি, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলসহ (বাসদ) আরও কয়েকটি দল এখন একটি বাম গণতান্ত্রিক জোট গঠনের চিন্তা করছে। তাদের লক্ষ্য হলো একতরফা নির্বাচনের রাজনীতির বিরুদ্ধে বিকল্প নির্বাচনমুখী ফ্রন্ট দাঁড় করানো। যদিও বাম দলের সংগঠনকাঠামো দুর্বল, তবু তাদের নৈতিক অবস্থান ও গণতন্ত্রের প্রশ্নে দৃঢ় অবস্থান ভোটারদের কিছু অংশে সাড়া ফেলতে পারে। বিশেষ করে শহুরে মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত যুবক এবং শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে বাম রাজনীতির একটি সংকেতমূলক গুরুত্ব এখনও রয়েছে।
তবে ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ কার্যত নিষিদ্ধ। এই প্রেক্ষাপটে নির্বাচনী রাজনীতির মাঠ ফাঁকা মনে করছে জাতীয় পার্টি। এই সুযোগে তারা সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা করছে। তাদের যুক্তি হলো, তারা একটি নিবন্ধিত দল, দেশের প্রধান কয়েকটি দলের একটি এবং বহু আসনে এখনও তাদের ভোটব্যাংক বিদ্যমান। অনেকে মনে করছেন, জাতীয় পার্টির ভেতরে যারা গুম, খুন, দমননীতি বা দুর্নীতির সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত নয়, বরং এখনও কোনোভাবে ন্যূনতম রাজনৈতিক সততা বজায় রেখেছেন, সামনে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণের পথ উন্মুক্ত থাকছে। আর এই তুলনামূলকভাবে গ্রহণযোগ্য অংশটি যদি নিজেদের পুনর্গঠন করতে পারে- দলের অতীত ভুলের দায় থেকে আলাদা হয়ে একটি গণতান্ত্রিক অবস্থান ঘোষণা করে- তবে তারা নতুন রাজনৈতিক জোট বা মঞ্চ গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে। তারা বিএনপি, জামায়াত বা গণতন্ত্র মঞ্চসহ অন্য কোনো বিরোধী শক্তির সঙ্গে কৌশলগত জোটে যুক্ত হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে।
বাংলাদেশের রাজনীতিতে জোটগুলো গঠিত হয় ক্ষমতার হিসাব-নিকাশে, নীতিগত ঐক্যে নয়। এ কারণে নির্বাচনের পর সেই জোটগুলো ভেঙে পড়ে, আর দলগুলো আবার নিজেদের পুরনো অবস্থানে ফিরে যায়।
তবু বর্তমান প্রেক্ষাপটে জোট রাজনীতি গণতন্ত্রের ন্যূনতম প্রাণশক্তি ধরে রাখার একমাত্র উপায়। কারণ দলগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন আয়োজনের সক্ষমতা না থাকলে পুরো রাজনৈতিক প্রক্রিয়াই অচল হয়ে যাবে। সুতরাং আগামী নির্বাচনের রাজনীতিতে মূল লড়াই হবে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব ও গণতান্ত্রিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য। যে দল বা জোট এই বাস্তবতা বুঝে জনজীবনের ইস্যুগুলো, যেমন- সংস্কার, মূল্যস্ফীতি, বেকারত্ব, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নাগরিক স্বাধীনতাকে সামনে আনতে পারবে, তারাই আসল শক্তি হয়ে উঠবে। অন্যথায় জোট গঠন, মুখবদলে রাজনীতির মৌলিক সংকট কোনোভাবেই বদলাবে না।
সবশেষে জনগণের প্রত্যাশার জায়গাটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘ দেড় দশকের রাজনীতিতে তারা ক্লান্ত। দলীয় দমন, দুর্নীতি, লুটপাট ও প্রশাসনিক অনাচারে বিশ্বাস হারিয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের হাতে তারা এখন একটি নতুন আশার আলো দেখছে, যেখানে ভোটের মাধ্যমে সত্যিকারের পরিবর্তনের সুযোগ আসতে পারে। তবে সেই আশাকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে দরকার রাজনৈতিক দলগুলোর আত্মসমালোচনা ও দায়িত্বশীলতা।
সানাউল্লাহ সাগর : কবি ও কথাসাহিত্যিক
মতামত লেখকের নিজস্ব
সূত্র ঃ আমাদের সময়