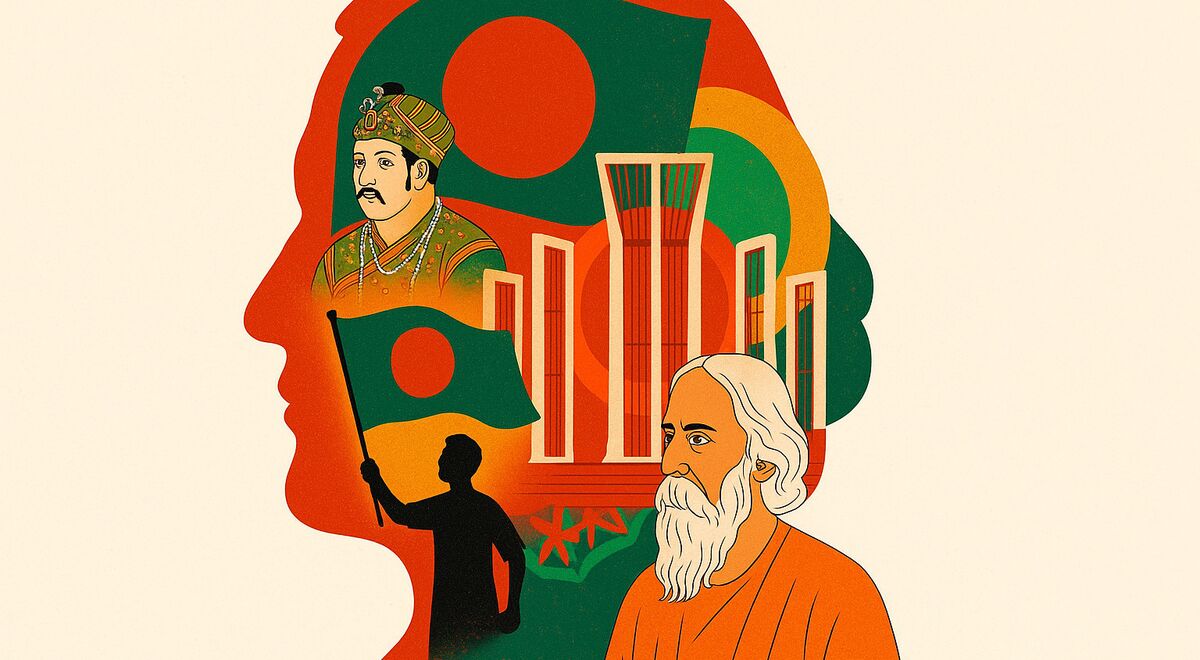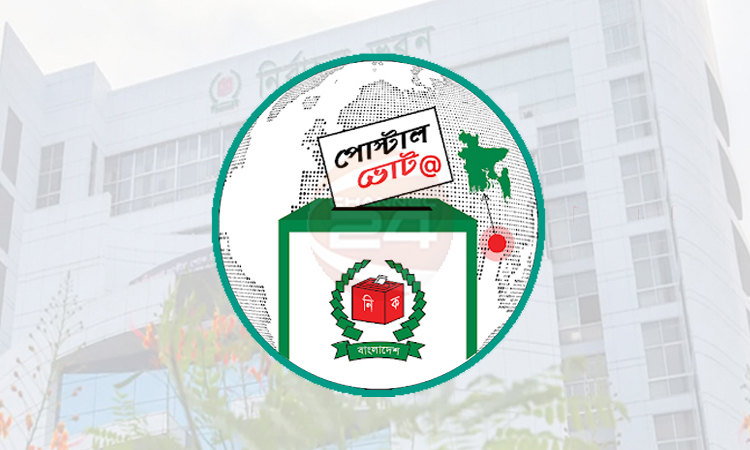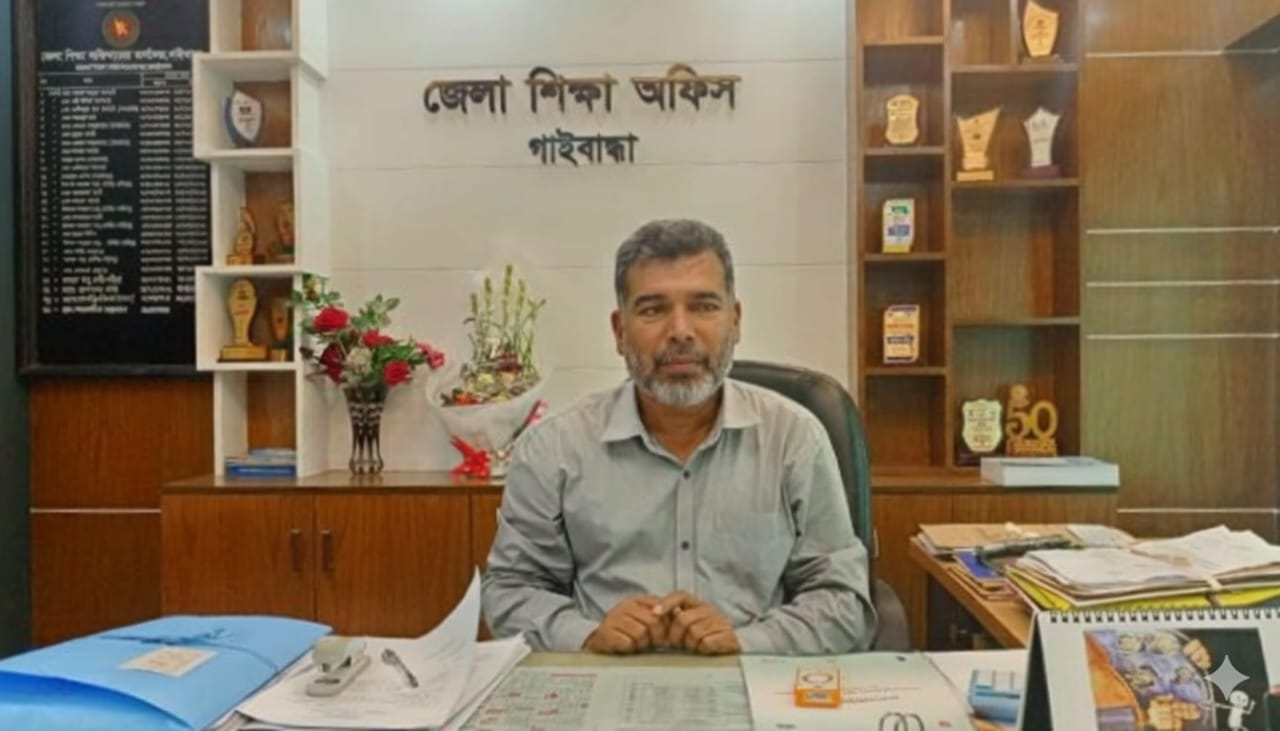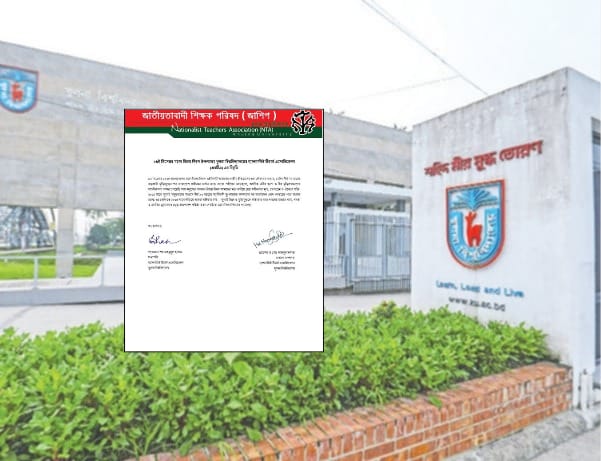|| মো. বশিরুল ইসলাম ||
দুই বিঘা জমিতে পেঁয়াজ চাষে সাইফুল শেখের খরচ হয়েছে দেড় লাখ টাকা। কিন্তু বিক্রি করে পেয়েছেন মাত্র ৫৮ হাজার টাকা। কষ্টের ফসলের দাম না পেয়ে ঋণ শোধের চিন্তায় ২৬ মার্চ মেহেরপুরের মুজিবনগরে সাইফুল শেখ (৫৫) পেঁয়াজ খেতেই বিষপান করে আত্মহত্যা করেছেন বলে তার মেয়ে রোজেফা খাতুন সম্প্রতি সংবাদ সম্মেলনে জানান। এর ঠিক ১৮ দিন পর ১৪ এপ্রিল রাজশাহীর বাঘা উপজেলার মাঝপাড়া বাউসা গ্রামের কৃষক মীর রুহুল আমিন (৭০) পেঁয়াজ চাষের লোকসান এবং ঋণের ভারে ট্রেনের নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছেন। দুই রেললাইনের মাঝে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। ট্রেন আসামাত্রই লাইনে শুয়ে পড়েন। এ আত্মহত্যার ভিডিও ভাইরাল হয়। সাইফুল শেখ ও রুহুল আমিনের এই ঋণ-কিস্তির ঘটনায় আসলে আমাদের দেশের কৃষকের অনেকাংশের চিত্র ফুটে ওঠেছে। এ রকম ঘটনা প্রায়ই কোথাও না কোথাও ঘটছে। কিন্তু কারো কোনো হেলদোল নেই। তারপরও কৃষকরা দেশের চাকা সচল রাখতে দিন-রাত পরিশ্রম করে ফসল উৎপাদন করে চলেছেন। দাবদাহ, শৈত্যপ্রবাহ, রোদ-বৃষ্টি, ঝড়-তুফান-যাই হোক, প্রতিদিন কাজ করতে হয় তাদের।
এসব কথা বলার কারণ হচ্ছে, যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন আজ সেই সব মেহনতি মানুষের প্রতীক মহান মে দিবস। বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন-সংগ্রামে অনুপ্রেরণার এক দিন। দৈনিক আট ঘণ্টা কাজ, আট ঘণ্টা বিশ্রাম ও আট ঘণ্টা বিনোদন এবং শ্রমের ন্যায্য মজুরির দাবিতে ১৮৮৬ সালের এই দিনে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে প্রায় ৪০ হাজার শ্রমিক সমবেত হন। সে সময় কারখানায় কোনো নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা বা বিশ্রাম ছাড়াই টানা কাজ করে যাওয়াটা স্বাভাবিক ছিল। পরবর্তী কয়েক দিনে এ আন্দোলনকে ব্যবসায়ী ও রাজনীতি মহল পছন্দ না করলেও, আরো হাজার হাজার ক্ষুব্ধ শ্রমিক ও আন্দোলনকারী এতে যুক্ত হতে থাকেন। আন্দোলনের এক পর্যায়ে পুলিশের গুলিতে অনেক শ্রমিক হতাহত হন। আন্দোলনের পুরোভাগে থাকা আট শ্রমিক নেতাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। এ ঘটনাগুলোর স্মরণে, ১৮৮৯ সালে ২০ দেশের সমাজকর্মী, শ্রমিক নেতা ও ট্রেড ইউনিয়নগুলোর আন্তর্জাতিক প্যারিস কংগ্রেসে বিশ্বব্যাপী মে মাসের ১ তারিখ ‘মে দিবস’ হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত হয়।
সেই থেকে প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী মে মাসের এক তারিখে শ্রমিকদের প্রতি সম্মান জানাতে মে দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। এটি শ্রমজীবীদের দিন হলেও দিবসটি সকল চাকরিজীবীর ছুটির দিন। কিন্তু কৃষক শ্রমিকরা জানেন না মে দিবসের ইতিহাস ও তাৎপর্য। এখন এ ইতিহাস শুধুমাত্র বইপত্র আর বক্তব্যের বিষয় হয়ে গেছে। বাস্তব জীবনে শ্রমিকের কাজের সময়, জীবনমান বা অধিকার কতটুকু উন্নত হয়েছে, সেটি ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। বিস্মিত হওয়ার কারণ- অর্থনৈতিক বৈষম্য, বাজারের অস্থিতিশীলতা এবং সরকারি সহযোগিতার অভাবে কৃষকেরা প্রায়ই দুঃখদুর্দশায় দিন কাটান। আত্মহত্যা কিংবা প্রতিবাদ করেও কৃষকের লাভ হচ্ছে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কৃষক তার কষ্টার্জিত ফসলের ন্যায্য দাম পান না এবং বছরজুড়ে সীমাহীন বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকেন। এরই মধ্যে বিশ্বে দেশে দেশে শ্রমিকদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষায় প্রণীত হয়েছে বহু আইন। বাংলাদেশেও শ্রমিকের স্বার্থের অনুকূলে অনেক আইন বলবৎ রয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক বাস্তবতা হলো সে আইনের বাস্তবিক প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত।
বর্তমানে মে দিবসের উদযাপন মূলত কিছু আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ। সরকারি ছুটি, কিছু বড় সমাবেশ, বক্ততা-বিবৃতি, সেমিনার, পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্র, প্রামাণ্য অনুষ্ঠান, টক শো এসব দিয়েই দায়সারা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, শ্রমিকের মৌলিক সমস্যা ও চ্যালেঞ্জগুলো এ আনুষ্ঠানিকতার আড়ালে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিক শ্রেণী তথা কৃষি শ্রমিকদের কথা থাকে উপেক্ষিত। আজও তারা ব্যস্ত সময় পার করছেন বোরো ধান কেটে মাড়াই করে ঘরে তুলতে। আমি নিজে কৃষক পরিবারের ছেলে। ফসল ফলাতে গিয়ে একজন কৃষকের কী রকম শ্রম ও অর্থের প্রয়োজন হয় তা আমার জানা। অথচ অনেক সময় কৃষক তার প্রকৃত উৎপাদন খরচও পান না। কৃষক হরতাল করতে পারে না, তারা দুর্বল কণ্ঠ নিয়ে তাদের ন্যায্যমূল্য ও ন্যায্য অধিকারের আন্দোলনও জানে না। তাই তো কৃষকরা আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন! কৃষকরা যে অবর্ণনীয় লোকসানের ঘূর্ণিপাকে আছেন, তা নিয়ে কোথাও কোনো আলোচনা আছে? আলোচনা হলেও তেমন লাভবান হচ্ছে না কৃষক। কৃষিতে কোনো নেতৃত্ব আছে কিনা, সেটাও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ফলে কৃষক ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিলে কিংবা আত্মহত্যা করলে কার কীই-বা আসে-যায়।
এখন নীতিনির্ধারকদের কাছে প্রশ্ন, কৃষির ওপর নির্ভরশীল এ দেশে কৃষকদের ভাগ্য নিয়ে এ খেলা আর কতদিন চলবে? আর কত কৃষকের আত্মহত্যার পরে চোখ খুলবে তাদের। গত বছর দীর্ঘতম খরা, পরবর্তী সময়ে বন্যা ও অতিবৃষ্টির কারণে শাক-সবজির উৎপাদন ব্যাহত হয়েছিল। অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গিয়েছিল মূল্য। পরে কৃষকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আশানুরূপ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। কিন্তু উচ্চমূল্যে জমি চাষ, শ্রমিকের মজুরি, বীজ, সার, কীটনাশক কিনতে গিয়ে ঋণের জালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যাচ্ছে অসহায় কৃষক। এসব করে অনেকেই পথে বসেছেন। কিছুদিন আগে আমরা ৮০ টাকা দরে আলু কিনেছিলাম। সে আলু এখন রাজধানীতে বিক্রি হচ্ছে ১৮ থেকে ২০ টাকা। অথচ ১ কেজি আলু উৎপাদনে যেখানে কৃষকদের খরচ হয়েছে ১৮ থেকে ২২ টাকা, সেখানে মাঠ থেকে বিক্রি হচ্ছে ১২ থেকে ১৫ টাকা দরে। পত্রিকায় দেখলাম কোথাও কোথাও তার চেয়েও কম দামে বিক্রি করতে হচ্ছে কৃষকদের।
ঢাকার খুচরা বাজারে এখন প্রতি কেজি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৫৫ থেকে ৬০ টাকায়। এক সপ্তাহের ব্যবধানে কেজিতে পেঁয়াজের দাম বেড়েছে ২০ টাকা পর্যন্ত। অথচ কিছুদিন আগেও বিক্রি হয়েছিল ৩০ থেকে ৩৫ টাকা। যা উৎপাদনের খরচের চেয়েও কম ছিল। এক কেজি পেঁয়াজের উৎপাদন খরচ হয়েছে প্রায় ৪০ টাকা। তাই তো দাম না পেয়ে সাইফুল শেখ ও রুহুল আমিন আত্মহত্যা করেছিলেন। এবারে রমজানে আমরা দেখেছি -আলু, পেঁয়াজ, টমেটো, কাঁচা মরিচসহ কিছু সবজিতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন ভোক্তারা। কিন্তু তাতে যে কৃষকের অশ্রু-দীর্ঘশ্বাস জড়িয়ে আছে, তা নিয়ে আমরা কি প্রশ্ন করেছি? পেঁয়াজ, আলু ও অন্যান্য সবজির পর এবার বোরো ধান উৎপাদনেও সফলতা পেয়েছেন কৃষকরা। কিন্তু এ সফলতার পরও তাদের কপালে দুশ্চিন্তার ভারি মেঘ ভর করতে শুরু করেছে। সরকার এবার কেজিতে চার টাকা বাড়ালেও ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা দেড় লাখ টন কমিয়েছে। এটা ঠিক, কৃষির উৎপাদন ব্যাপক বাড়লেও সুষ্ঠু বিপণন, পরিবহন ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে না ওঠায় জিম্মি হয়ে পড়ছেন চাষীরা। তাই তো, উৎপাদন যত ভালোই হোক না কেন, ফসলের ন্যায্যমূল্য না পেলে কৃষকের জন্য তা সোনার ফসল হয় না, বরং গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়।
কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে হলে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের সরাসরি বাজারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। পণ্য পরিবহনকালীন চাঁদা বন্ধ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমাণ পণ্য সংগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। কৃষকের ফসল বিক্রির সুবিধার্থে ইউনিয়ন পর্যায়ে বিপণন সেবা চালু করা, উপজেলা পর্যায়ে মিনি হিমাগার স্থাপন এবং জেলা পর্যায়ে কৃষক বাজার বা প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন করা গেলে কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির সংকট দূর হবে বলে আশা করা যায়। তাই উপজেলা পর্যায়ে কৃষি বিপণন কর্মকর্তার জনবল সহ একটা পূর্ণাঙ্গ সেটআপ দরকার। সে পরিকল্পনাও সরকারের রয়েছে। এরই মধ্যে কৃষি উপদেষ্টা এ ব্যাপারে বেশ উৎসাহী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। আবার যেহেতু মৌসুমে জোগান বেশি থাকলে কৃষিপণ্যের দামও কমে যায়, কিন্তু অমৌসুমে উৎপাদিত পণ্যে কৃষক ভালো দাম পায়। তাই কৃষকদের অমৌসুমে ফসল উৎপাদনের ওপর বেশি জোর দিতে হবে। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের জন্য শস্য বীমা চালু, ফসলহানি হলে ঋণ মওকুফের ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রক্রিয়াজাতকারীদের সঙ্গে কনটাক্ট ফার্মিংয়ের মাধ্যমে চাহিদা ভিত্তিক পণ্য উৎপাদন করলে ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি সহজ হয়। কৃষকদের আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি এবং বাজার সম্পর্কে সচেতন করার জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করতে হবে।
প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতি থেকে কৃষককে রক্ষা, ক্ষেত্রবিশেষে বিদেশ থেকে অবাধ আমদানি না করা, কৃষক ও ভোক্তাবান্ধব আমদানি শুল্ক বসানো এবং ফসল সংরক্ষণের ব্যবস্থা বাড়ানো জরুরি। সরবরাহ ব্যবস্থায় মধ্যস্বত্বভোগীদের নিয়ন্ত্রণে রাখাও দরকার। আসলে কৃষকের চাই ফসলের ন্যায্যমূল্য। ভোক্তার চাই সুলভ মূল্যে নিরাপদ খাদ্য। মোটা দাগে এ দুটি বিষয় নিশ্চিত করাই এখন সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। খাদ্যের উৎপাদন বাড়ানোর চ্যালেঞ্জ দেশ অনেকটাই পেরিয়ে এসেছে।
কৃষির দেশে কৃষকের আত্মহত্যার হৃদয়বিদারক ঘটনাটি শুধু একটি বিচ্ছিন্ন ট্র্যাজেডি নয়, বরং এটি লজ্জাজনক। কৃষক সাইফুল শেখ ও রুহুল আমিনের আত্মহত্যা এমনি এমনি ঘটেনি। তার কারণ খুঁজে কৃষিপণ্যের উপযুক্ত মূল্য যেন কৃষক পায় তার ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে গ্রহণ করতে হবে। রাষ্ট্রকে নানামুখী অর্থনৈতিক ভর্তুকি ও প্রণোদনা দিয়ে বাঁচাতে হবে আমাদের দেশের কৃষি শিল্পকে, আর বাঁচিয়ে রাখতে হবে এ দেশের উজ্জ্বল সন্তান কৃষকদের। নয়তো কোনো একদিন খাদ্যের তীব্র সংকটে নাজেহাল হবে দেশ।
লেখকঃ কৃষিবিদ ও উপ-পরিচালক, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়