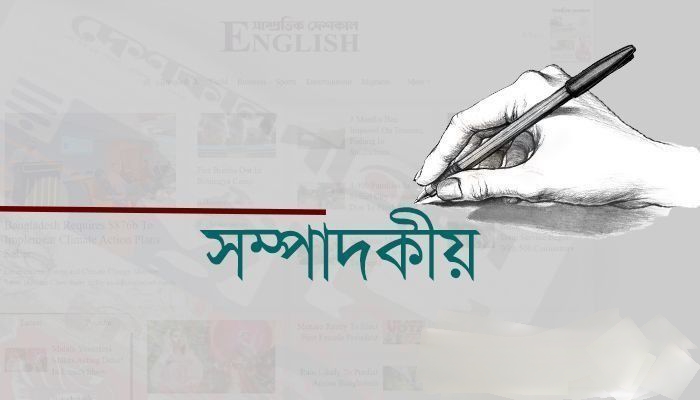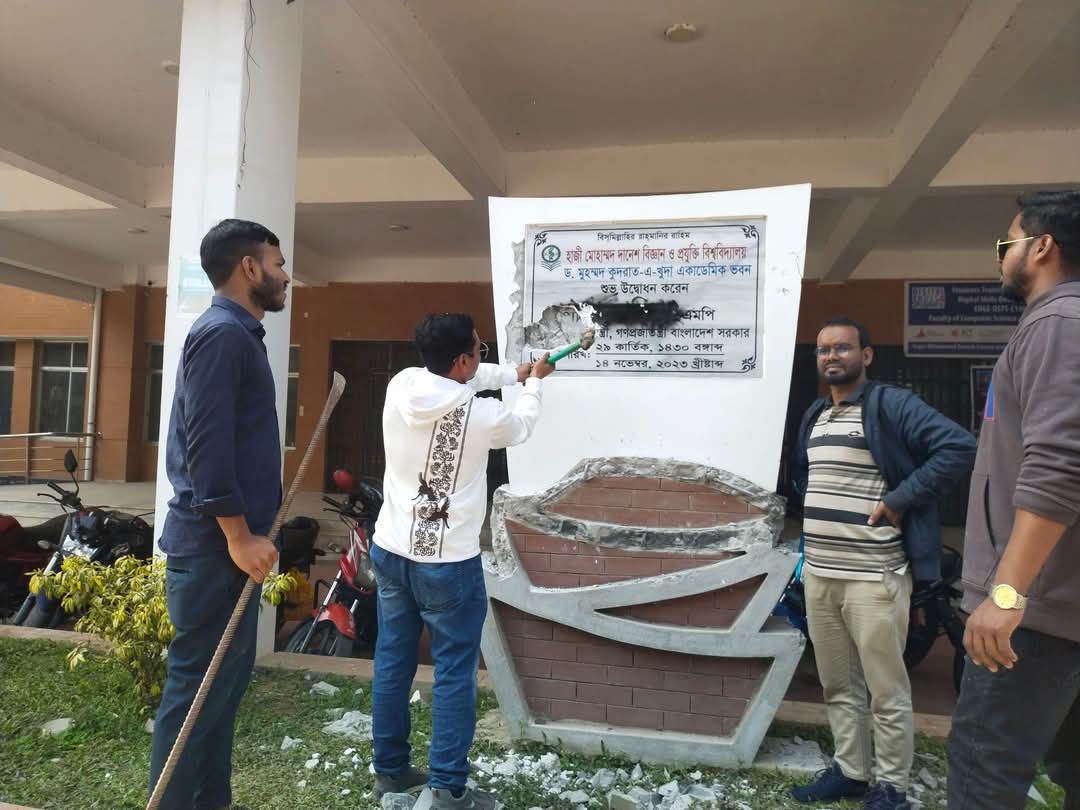আশফাক সফল,
কয়েক দিন আগে ১১ বছর বয়সী এক কিশোরীর নিরুদ্দেশ এবং পরে তার উদ্ধারের ঘটনা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা চলছিল। বিভিন্ন গণমাধ্যম থেকে জানা যায়, মায়ের চিকিৎসার জন্য মাস দুয়েক আগে সপরিবারে ঢাকায় আসা দক্ষিণাঞ্চলের এই কিশোরী নিখোঁজ হন মোহাম্মদপুরের একটি শপিং মলের কাছ থেকে। পরবর্তী সময়ে তথ্যপ্রযুক্তি সহায়তা নিয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তার সন্ধান পান দেশের উত্তরাঞ্চলের একটি জেলায়।
দক্ষিণাঞ্চলের এক কিশোরী কীভাবে উত্তরাঞ্চলের একটি জেলায় পৌঁছে গেলেন এবং তার এই পৌঁছে যাওয়ার পিছনে কার বা কাদের হাত রয়েছে সেটি বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সোশ্যাল পুলিশিংয়ে ব্যস্ত হয়েছেন নেটিজেনদের অনেকেই। ক্ষেত্রবিশেষে কিশোরীর পরিবারকে নিয়ে মন্তব্য এবং সমালোচনায় উত্তপ্ত ছিল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো।
ঠিক করে বললে সুশীল সমাজের কিছু সদস্যের মন্তব্য এবং পোস্ট ছাড়া প্রায় সব ছিল ওই কিশোরী বা তার পরিবারকে দোষী প্রমাণ করার মিডিয়া ট্রায়াল মাত্র।
এটি শুধু একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং এটি ডিজিটাল যুগে অভিভাবকত্বের চ্যালেঞ্জ, কিশোর-কিশোরীদের মানসিকতা এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রভাব সম্পর্কে গভীরভাবে ভাবার সুযোগ করে দিয়েছে। এর আগেও আমরা দেখেছি, গত বছর রাজধানীর মেরাদিয়ার নোয়াপাড়া এলাকার তিন কিশোরী ঘর ছাড়েন দক্ষিণ কোরিয়া যাওয়ার লক্ষ্য নিয়ে। ঢাকা থেকে গাজীপুরে চলে যাওয়া ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ুয়া তিনজনের পরিকল্পনা ছিল গার্মেন্টসে চাকরি করে যে টাকা পাবে তা দিয়ে কোরিয়ার বিটিএস ব্যান্ড দলের সদস্যদের কাছে চলে যাবে।
এছাড়া টিকটক, ফেসবুকসহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে পরিচয় ও পরবর্তীতে প্রলোভনের মাধ্যমে নারী, কিশোর-কিশোরী, শিশু পাচারের ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে গত কয়েক বছরে।
উল্লেখ্য, ২০২১ সালে এরকম একটি পাচার চক্রের ১১ সদস্যকে গ্রেফতার হয়, যারা কিশোর-কিশোরীদের প্রলুব্ধ করে ভারতে পাচার করতো।
শুধু তরুণী, কিশোরী ও মেয়ে শিশুরা নয়, অনেক ক্ষেত্রে ছেলেশিশু ও কিশোরদের পাচার, অপহরণের ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ-মিডিয়ার জন্য ভিডিও ক্লিপ, রিল ইত্যাদি তৈরি করা নিয়ে সংঘাতের সংবাদ চোখে পড়ার মতো।
২০২১ সালে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলায় টিকটক ভিডিও তৈরির জন্য স্থানীয় কিশোরদের মধ্যে বিরোধের জেরে সংঘর্ষ ঘটে। ওই সংঘর্ষে কয়েকজন আহত হয় এবং পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ধরনের ঘটনা কিশোরদের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের নেতিবাচক প্রভাব এবং সহিংস প্রবণতার দিকে ইঙ্গিত করে।
দুর্বল প্যারেন্টিং ও সাইবার দুনিয়া
আধুনিক প্রযুক্তির বিস্তার অভিভাবকত্বকে আগের যেকোনও সময়ের চেয়ে বেশি জটিল করে তুলেছে। বিশেষ করে করোনা মহামারির পর থেকে অনলাইন শিক্ষা এবং ডিজিটাল ডিভাইসের ব্যবহার কিশোর-কিশোরীদের হাতে বেড়েছে। অন্যদিকে, অনেক অভিভাবকেরই প্রযুক্তি সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান নেই, যার কারণে কঠিন হয়ে পড়েছে সন্তানদের অনলাইন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করা।
উন্নত জীবনযাত্রার প্রয়োজনে এবং শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের ক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন ধরনের নির্ভরশীলতা, বিশেষ করে কোভিড এবং কোভিড-পরবর্তী সময়ে অনলাইন ক্লাস বিভিন্ন কারণে মোবাইলে এবং ইন্টারনেটের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে আমাদের দেশে।
উল্লেখ্য, বাংলাদেশের কোভিডের আক্রমণ হয়েছিল ২০২০ সালের মার্চ মাসে। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারের উদ্যোগে চালু হয় অনলাইন ক্লাস ও বিভিন্ন অ্যাসেসমেন্ট পদ্ধতি, যার ফলে শিক্ষার্থীদের হাতে অভিভাবকরা বাধ্য হন মুঠোফোন বা এ জাতীয় কোনও ইলেকট্রনিক এবং কমিউনিকেশন ডিভাইস হাতে তুলে দিতে।
২০২৩ সালে বাংলাদেশের পটভূমিতে ইউনিসেফের করা এক জরিপ অনুযায়ী, ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সী ১১ হাজার ৮২১ জন কিশোর-কিশোরীর মধ্যে ৮১.২ শতাংশ প্রতিদিন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সময় ব্যয় করে এবং ৯০ শতাংশ মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের শেষে নভেম্বরে দেশে মোবাইল সংযোগের সংখ্যা প্রায় ১৯ কোটি এবং এর মধ্যে ১১ কোটির বেশি আছে ইন্টারনেট সুবিধা। ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১২ কোটি ৬৬ লাখ; গত বছরের শুরুতে যা ছিল ১০ কোটির ঘরে। বিজ্ঞাপনী সংস্থা ন্যাপলিয়ন ক্যাটের মতে, বাংলাদেশ ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৬৬ লাখের বেশি; এবং ব্যবহারকারীদের প্রায় অর্ধেক তরুণ।
অন্যদিকে ২০২৪ সালের তথ্য অনুযায়ী টিকটক ব্যবহারকারীদের সংখ্যার হিসাবে বাংলাদেশের অবস্থান দশম; ৪১ লাখের বেশি টিকটক আছে বাংলাদেশিদের। মোটা দাগে, বাংলাদেশে ডিজিটাল সংযোগের গভীরতা এখন অনেক বেশি। তবে এই সংযোগ কি নিরাপদ, তা একটি বড় প্রশ্ন।
সম্প্রতি সাইবার অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ২০২৩ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা যায়, দেশে প্রায় ৭৮ শতাংশ কিশোর-কিশোরী অনলাইনে ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছে। ঘটনার গভীরে থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় অভিভাবকদের দুর্বল প্যারেন্টিংয়ের কারণে তারা নিজেদের সন্তানদের অনলাইন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে ব্যর্থ হচ্ছেন, যার ফলে সন্তানেরা শিকার হচ্ছে বিভিন্ন অপরাধের এবং ক্ষেত্রবিশেষে অপরাধ চক্রে জড়িয়ে পড়ছে।
দুর্বল প্যারেন্টিং যখন বলা হচ্ছে এখানে অভিভাবকের স্বেচ্ছা বা সদিচ্ছার কোনও অভাবকে নির্দেশ করা হচ্ছে না (আমি এই প্রবন্ধে সেরকম কোনও আলোচনা উপস্থাপন করছি না)। এখানে দুর্বল প্যারেন্টিংয়ের কারণ হিসাবে সাইবার লিটারেসির অভাব এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতার ঘাটতিকে আলোচনায় আনা হচ্ছে।
সাইবার সচেতনতার অভাব
বিগত কয়েকটি বছর ধরেই সাইবার লিটারেসির বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে সমাজবিজ্ঞানী এবং তথ্য-প্রযুক্তিবিদদের মধ্যে। শহরাঞ্চলে মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত অভিভাবকদের কাছে তথ্যপ্রযুক্তি এবং তথ্য প্রযুক্তির ডিভাইসগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে কিছুটা (এবং ক্ষেত্রবিশেষে বেশ ভালো রকমের) জ্ঞান থাকলেও মফস্বল এবং গ্রামীণ অঞ্চলে এ বিষয়ে তেমন কোনও ধরনের সাইবার লিটারেসির বৃদ্ধির উদ্যোগ কখনোই নেওয়া হয়নি। ফলশ্রুতিতে, আমাদের বেশিরভাগ অভিভাবক কোনও ধরনের অভিজ্ঞতা এবং গভীর ধারণা ছাড়াই ডিভাইস ব্যবহার করতে শুরু করেন বা ব্যবহার করতে সুযোগ করে দেন আমাদের কিশোর কিশোরীদের।
আজ থেকে চার বছর আগে (কোভিড এবং কোভিড-পরবর্তী সময়কালে) যখন এভাবে তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার করতে হয়, তখন যেই কিশোর-কিশোরী এবং শিশুদের কাছে এই ডিভাইসগুলো কানেক্টিভিটি পৌঁছে গেছে তারাই কিন্তু আজকে রয়েছে বয়ঃসন্ধিকালে।
অনিয়ন্ত্রিত ইন্টারনেট ব্যবহার
বাংলাদেশে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে ইন্টারনেটের ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) পাবলিক হেলথ ও ইনফরমেটিক্স বিভাগের এক গবেষণায় দেখা গেছে, দেশের গ্রামীণ এলাকায় ১১ থেকে ১৭ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে প্রায় ৩৩ শতাংশ ইন্টারনেট ব্যবহার করে, এবং তাদের মধ্যে শতকরা ৫৯ শতাংশ কমপক্ষে একবার সাইবার হেনস্তার শিকার হয়েছেন। তারা মূলত ট্রলিং, বুলিং, ব্যক্তিগত ছবি চাওয়া ও পর্নোগ্রাফির শিকার।
সাম্প্রতিক সময়ে অবস্থার আর কিছু অবনতি হয়েছে। স্ন্যাপ ইনকরপোরেটেডের ডিজিটাল ওয়েলবিয়িং ইনডেক্স-২০২৩-এর তথ্য অনুযায়ী, ১৩ থেকে ২৪ বছর বয়সীদের মধ্যে ৭৮ শতাংশ অনলাইনে ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় ২ শতাংশের বেশি।
উল্লেখ্য, প্রযুক্তির দ্রুত বিস্তারের কারণে মুঠোফোন ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীরা সহজেই অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য অনুপযুক্ত কনটেন্টের সংস্পর্শে আসছে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক আসাদুজ্জামানের করা এক গবেষণায় দেখা গেছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ৪২ শতাংশ স্কুল শিক্ষার্থী (যাদের বেশিরভাগই মেয়ে) সেক্সটিং, সাইবার বুলিং, অপমানজনক ভাষা এবং অশ্লীল মন্তব্য পাওয়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করছেন। ফলে তাদের অনেকেই এই প্ল্যাটফর্মগুলো ব্যবহারের জন্য বা এই ধরনের বার্তার জন্য তারা খারাপ অনুভব করেন।
এছাড়া গবেষণা চলাকালীন সাক্ষাৎকারে শতকরা ৯২ ভাগ শিক্ষার্থী বলেছে যে তারা এই প্ল্যাটফর্মে সেক্স ক্লিপ দেখে।
কিশোর-কিশোরীদের মানসিক প্রেক্ষাপট
বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীরা দ্রুত শারীরিক এবং মানসিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়। আবেগপ্রবণতা, নতুন সম্পর্কের প্রতি আকর্ষণ, এবং নিজের পরিচয় (self identity) প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা তাদের অনলাইনে ঝুঁকির দিকে ঠেলে দেয়।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, যেমন- টিকটক, ইনস্টাগ্রাম এবং ইউটিউব কিশোর-কিশোরীদের জীবনে বিশাল প্রভাব ফেলছে। এসব প্ল্যাটফর্মে দেখা চাকচিক্যের সঙ্গে বাস্তবতার ফারাক তারা বুঝতে পারে না।
এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রচুর সংখ্যক কিশোর-কিশোরীরা বলেছেন, তারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কনটেন্ট অনুসরণ করেন, এবং সেই হিসাবে নিজেদের ফ্যাশন-স্টাইল সেট করে। অনেকেই প্ল্যাটফর্মে জনপ্রিয়তার জন্য বিভিন্ন ভিডিও কনটেন্ট তৈরি এবং শেয়ার করে।
মূলত এভাবেই তারা বিলাসী জীবনযাত্রা এবং জনপ্রিয়তার প্রতি আকর্ষিত হয়ে বিভ্রান্ত হচ্ছেন।
উত্তরণের পথ
ডিজিটাল যুগে অভিভাবকত্বের চ্যালেঞ্জগুলোর মোকাবিলায় কিশোর-কিশোরীদের মানসিক প্রেক্ষাপট, সাইবার কনটেন্টের প্রভাব এবং সর্বোপরি সাইবার লিটারেসি গুরুত্বপূর্ণ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। শুধু অভিভাবকদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা নিয়ে সমালোচনা না করে, সমাজের প্রতিটি স্তরের সচেতনতা বাড়িয়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। কিশোর-কিশোরী ও অভিভাবকদের সঙ্গে আলাদা করে সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কিত আলোচনার যেমন দরকার আছে; তেমনি সরকার ও প্ল্যাটফর্ম কর্তৃপক্ষকে কিশোর-কিশোরীদের জন্য নিরাপদ অনলাইন পরিবেশ নিশ্চিত করতে এগিয়ে আসতে হবে। একই সঙ্গে পরিবারের মধ্যে আন্তরিকতা ও বিশ্বাস বৃদ্ধি করে কিশোর-কিশোরীদের সাথে খোলামেলা আলোচনার পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন।
আমাদের সন্তানদের নিরাপদ ও সুস্থভাবে গড়ে তুলতে, ডিজিটাল যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অভিভাবকসহ সব অংশীজনকে এগিয়ে আসতে হবে।
লেখক: ব্লগার ও আইটি প্রফেশনাল; যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটরস ফোরাম।